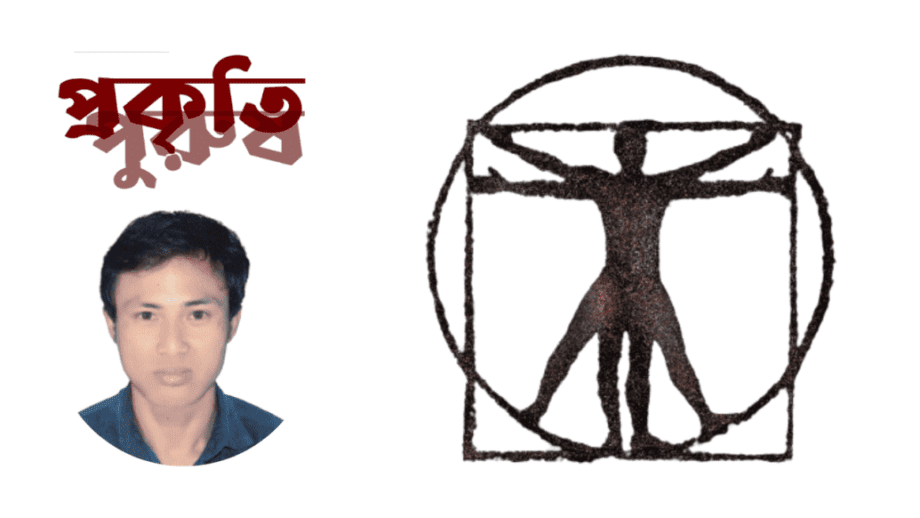এই রচনাটা কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী রচিত ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসরণ করে লেখা হয়েছে। আমরা বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরেজী বিভিন্ন ভাষার অভিধান খুললে চাকমা শব্দের সাক্ষাৎ পাই। এই যুগের ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছেন যে, বর্ত্তমান পৃথিবীর সমস্ত ভাষা, যাহার সংখ্যা ৬০০০, আসলে একৈ আদি মহাভাষা থেকে ক্রমবিচূর্নীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে।১ সেজন্য বিষু, বিজু, ফুল, মূল এবং গজ্যেপজ্যে শব্দগুলার অর্থ জানার জন্য “বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ”-এর নিয়ম অনুসরণ করেছি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় কথা বলতেন। প্রাচ্যের ভাষাতত্ত্বে শব্দের ভিতরে শব্দের অর্থ আছে, শব্দের সঙ্গে তাহার অর্থ দেহ ও আত্মার ন্যায় ওতপ্রোত বা ‘তাদাত্ম্যক’— ভারতীয় পণ্ডিতগণের এইরুপ ধারণা খ্রীস্টপূর্ব্ব ৪০০-এর বহু আগে থেকেই সার্ব্বিকভাবে প্রচলিত ছিল২ বলে এই খবর আমরা জানি। কলিম খান বলেছেন— “অর্থের সংবাদ নেবার জন্য শব্দের বাহিরে যেতে হৈত না, শব্দের ভিতরে থাকালেই চলত। কেননা শব্দার্থ বের হৈত শব্দের ভিতর থেকে, তাহার বুৎপত্তি দেখে”।৩ আর এখন আমাদের “সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পাশ্চাত্যের এই প্রতীকী (অ্যারবিট্রারী) রীতির প্রভাব বেড়ে যায় এবং এমন হয় যে আধুনিক(?) যুগে পৌঁছে দেখা যায় প্রাচ্যের ভাষাগুলাও নিজেদের চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের আরবিট্রারী শব্দার্থ রীতিকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে। কাজেই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থবিধি অনুসরণ করে শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করে শব্দের মানে জেনে সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। …
বিষু:
√বিষ্+ উ = বিষু।
√ব্ + ই + ষ্ + উ = বিষু।
√বহন + গতিশীল/সক্রিয়ন + দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন + (নবরূপে) উত্তীর্ণন।
বিষু-এর ক্রিয়ামূল √বিষ্। বিষ্ মানে সক্রিয়ন/গতিশীল বহন দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন। আবার, বিষ্ (নবরূপে) উত্তীর্ণন কিংবা ‘উ’ হলে সে আর বিষ থাকে না, হয়ে যায় বিষু (√বিষ্ + উ)। সেজন্য বঙ্গীঁয় শব্দার্থকোষ বিষুকে বলেছেন ‘সাম্য’। তারমানে চেতনাজগৎ, জ্ঞানজগৎ এবং যে কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ভাবে একতাবোধকে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে সক্রিয়ন/গতিশীল বহন দিশাগ্রস্ত শক্তিযোজন নবরূপে উত্তীর্ণন করাই বিষু।
বিজু:
√বিজ্ + উ = বিজু
√ব্ + ই + জ্ + উ = বিজু
√বহন + গতিশীল/সক্রিয়ন + জনন + (নবরূপে) উত্তীর্ণন = বিজু।
√বিজ্ + উ। বিজ্ মানে সক্রিয়ন/গতিশীলবহন জনন। আবার, বিজ্ (নবরূপে) উত্তীর্ণন কিংবা ‘উ’ হলে সে আর বিজ্ থাকে না, হয়ে যায় বিজু (√বিজ্ + উ)। বিষুর মতৈ একইভাবে চেতনাজগৎ, জ্ঞানজগৎ এবং যে কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ভাবে একতাবোধকে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে জনন করাই হলে বিজু।
এই বিজুর ফলে যে নতুন বৎসরের আগমন হয় তহার ফলে বর্ত্তমানের যে দিন আমাদের বহন করছে তাহা নতুন ভাবে গতিশীল/সক্রিয়ন হবে এবং তাহার ফলে আমাদের জীবনযাপনে (প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে) নতুন ভাবে উত্তীর্ণন হবে জনন্ ক্রিয়া … বিজ্ (নবরূপে) উর্ত্তীণন না হলে আমাদের জীবনে কোন সফলতা আসবে না, তাই বিজকে (নবরূপে) উত্তীর্ণন করতে হয়, আমাদের মঙ্গল সাধনে যাহা প্রকৃতি করছে … প্রকৃতির (নবরূপে) উত্তীর্ণন ক্রিয়াকে আমরাও স্মরণ করছি— একজন ইঞ্জিনিয়ার যেমন বিল্ডিং তোলার আগে নক্সা অঙ্কন করে, ঠিক তেমনি পূর্ব্বপুরুষেরা বিজুকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে নক্সা অঙ্কন করে—ফুল বিজু, মূল বিজু এবং গজ্যেপজ্যে দিনগুলো হলনক্সা অঙ্কনের কাজের প্রতিফলন মাত্র অর্থাৎ চেতনা জগৎ, জ্ঞান জগৎ বা যে কোন সৃষ্টিশীল কর্ম্মৈ হোক না কেন ফুল, মূল এবং গজ্যেপজ্যে উৎসবের আয়োজন হচ্ছে সে সব সৃষ্টিশীল কর্ম্মের প্রতিফলন। মারমাদের সাংগ্রাই, ত্রিপুরাদের বৈসুক, তঞ্চঙ্গ্যাঁদের বিষু এবং ভারতের আসাম রাজ্যের অসমীয়দের বিহু উৎসব হচ্ছে এক্ষণ নিঃসন্দেহে জাতীয় উৎসব।
ফুল বিজু:
√ফুল = ফ্ + উ + ল = পালনস্থিতি + (নবরূপে) উত্তীর্ণন + লালক।
√বিজু = ব্ + ই + জ্ + উ = বহন + গতিশীল/সক্রিয়ন + জনন + (নবরূপে) উত্তীর্ণন।
আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থাৎ আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আত্মবিচ্ছেদ হওয়ার কারণে আমরা আমাদের স্বরুপ চিনতে পারি না। তাহলে ফুল বিজুর ফুল কী? এর উদ্দেশ্য কী? কিসের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বপুরুষরা ফুল বিজু পালন করেছিলেন? এরকম প্রশ্ন করলে যে কোন একটা উত্তর বেরিয়ে আসবে। কারণ যে কোন ঘটনার পিছনে একটা কারণ থাকে। আমরা পাশ্চাত্যের মত প্রতীকী ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে ফুল বিজুর “ফুল”কে দৃশ্যলোকের প্রাকৃতিক ফুল মনে করি। আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের প্রধান সমস্যা(!) ছিল অদৃশ্য কিন্তু সমাজে অত্যন্ত সক্রিয় বিষয়কে মুখের ভাষায় কথা বলে বোঝানো।৫ যা হোক এক্ষণে আমরা ফুল কী সেটা বুঝার জন্য সেদিকে এগিয়ে যাব। বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ মতে— ফুল এর ক্রিয়ামূল ফুল্ল। ফুল্ল মানে পালনস্থিতির (নবরূপে) উর্ত্তীনন লালন-লালক। ফুল শব্দের অর্থ— “কোন সত্তার ইচ্ছাদির বস্তুগত রূপ লাভ করে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হয়ে সত্তা থেকে বেরোনো এবং নির্গমণ পথের শেষে পৌঁছে বিচিত্র রূপে অপেক্ষা করাকে বলা হয় ফুল ক্রিয়া; এবং সেরকম ক্রিয়া করে যে তাকে ফুল বলে”।৬ তারমানে ফুল বিজু দিনটা হচ্ছে এমন একটা দিন, যে দিনে শুধু একটাই চাওয়া কিভাবে ফুলে ওঠব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ফুলে ওঠার জন্য ফুল বিজু উৎসব আয়োজন করেছিলেন। ফুল শব্দ দিয়ে চাকমা ভাষায় অনেক কথা আছে। যেমন: পাণিয়ান ফুলি উত্তে অর্থাৎ পাণি ফুলে উঠেছে। কিয়াগান ফুলি উত্তে অর্থাৎ শরীর ফুলে উঠেছে। লক্ষ্য করুন পাণি, শরীর কিভাবে ফুলে ওঠে বা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমরা নিশ্চিত বলতে পারি ফুল বিজুর ফুল শব্দটী প্রাকৃতিক ফুল নয়— আমাদের জীবনাচারের ফুল, যাহা (জীবনের কলি থেকে) ফুলে ওঠে … প্রাকৃতিক ফুল-ও (কলি থেকে) ফুলে ওঠে— ফুল হচ্ছে জ্ঞান, চেতনা বৃদ্ধি করা এবং পরিবার সমাজ যেন উন্নত হয় সম্মিলিতভাবে সেই লক্ষ্যে নিয়ে উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে ফুল বিজু। ফুল বিজুর প্রাকৃতিক ফুল হল জীবনাচারের ফুলের প্রতীকীরূপ। জীবনাচারের ফুলকে ভুলে গিয়ে শুধু বিজুর প্রাকৃতিক ফুলকে মনে রাখলে জীবন এক সময় উত্তরহীন হয়ে যায়— আজ যাহা দৃশ্যমান। পূর্ব্বপুরুষের চাওয়া-পাওয়া থেকে আত্মবিচ্ছেদ হয়ে যে ফুলকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সমৃদ্ধির পথ রচনা করি এক্ষণ আমরা সেই ফুলকে শুধু প্রাকৃতিক ফুল মনে করি। এমনকি নিম্ন-অধিকারীগণের হাতে পড়ে ফুল বিজুর দিনে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করা পর্য্যন্ত থেমে থাকেনি শেষ পর্য্যন্ত ফুল ভাসানো উৎসবে পরিণত হৈল ফুল বিজু।
গত একশত/দুইশত বছর আগে ফুল বিজুর স্বরূপ কী ছিল তা আমরা জানতে পারি শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত “চাকমা জাতি” গ্রন্থে। তিনি উক্তগ্রন্থে ফুল বিজু সম্পর্কে বলেছেন— “ফুল বিষু অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্বদিন হতে ইহাদের তীর্থকার্য আরম্ভ হয়। প্রথমে স্নানাদিতে শুচি হয়ে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত বারান্দায় বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ঘুরিয়া আকুল প্রাণে বুদ্ধ নাম কীর্তন করিতে থাকে। এরূপে কিছুকাল প্রদক্ষিণের পর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক মহামুনির শ্রীচরণ প্রান্তে উপচার-থালা এবং প্রজ্জলিত বর্তিকা স্থাপন করত: ভূমীগত প্রণিপাত করে”। … অতপর আরো লিখেছেন— “বিষু সম্বন্ধে এতক্ষণ করিয়া যাহা লিখিত হল, তৎসমস্তই মহামুনি- সম্পৃক্ত”। ঘোষ মহাশয়ের বয়ানগুলা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেকালে ফুল বিজু কিরূপ ছিল আর আজকের একশত/দুইশত বছরের ব্যবধানে বিজু কিরূপে পালিত হচ্ছে! সেজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় ঊনিশ শতকের তাহার-ও … তাহার-ও আগে ফুল বিজু পালিত হয় উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার বয়ানকৃত অনুসারে। ফুল শব্দটা আমাদের প্রমাণ দিচ্ছে যে পূর্ব্বপুরুষের চিন্তাধারা থেকে যুগে যুগে আত্মাবিচ্ছেদ হয়েছি। যেমনটা ফুল বিজুর মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য চেতনাগত, জ্ঞানগত ফুলে তোলা থেকে আত্মবিচ্ছেদ হয়ে ধর্ম্মীয় কার্য্যে রুপান্তরিত হওয়া, ধর্ম্মীয় কার্য্য থেকে আত্মবিচ্ছেদ হয়ে গঙ্গাঁদেবীর উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করা, গঙ্গাদেবীকে ফুল নিবেদন করা থেকে আত্মবিচ্ছেদ হয়ে ফুল ভাসানো উৎসবে পরিণত হওয়া। অবশ্য এক্ষণো গজ্যেপজ্যে দিনে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে বুদ্ধপূজা করা হয়। তবে এ স্থলে মনে রাখা উচিৎ গজ্যেপজ্যে মানে পহেলা বৈশাখ নয়। গজ্যেপজ্যে হচ্ছে একটা সত্ত্বা, সেই সত্ত্বার নামানুসারে গজ্যেপজ্যে শব্দের নামকরণ। এই বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।
মূল বিজু:
√মূল = ম্ + উ + ল = মিতি + (নবরূপে) উত্তীর্ণন + লালক।
√বিজু = ব্ + ই + জ্ + উ =বহন + গতিশীল/সক্রিয়ন + জনন + (নবরূপে) উত্তীর্ণন।
মূল শব্দটা নিয়ে প্রধান সমস্যা। কেউ বলে মূল আর কেউ বলে মুর। শব্দগুলার অর্থ নিষ্কাশন না করে বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ এর ব্যাখ্যা দেখে সঠিক শব্দটা আমরা চিনে নিতে পারব। বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ মূল শব্দটার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন— মূ লালিত যাহাতে। এই মূ হৈল সত্ত্বার নিগমযোগ্য সারমর্ম্মের আধার। একেই আমরা বলেছি ‘মিতির নবরূপী উর্ত্তীণ/আধার”।৮ অপরদিকে মুর শব্দটার অর্থ দিয়েছেন— “কেন্দ্রে সীমায়িত সত্ত্বার ‘কেন্দ্র থেকে পেরিয়ে যাওয়া’ এবং সেভাবে কোন আধারের মধ্যে থাকা। স্বভাবতই এ হৈল ‘নিগম্য-সারাৎসার রহে যাহাতে’। ফলত এ’টী জ্ঞান ও ধনের অন্যত্রগামী হৈতেই পারে। তারমানে, সেকালে যে সত্ত্বা জ্ঞান, পণ্য ইত্যাদি নিয়ে বাইরে যেত, তাদের মুর বলা হয়ে থাকবে”।৯ চাকমা জাতির বহুল প্রচলিত একটি কথা আছে রেত্তু এলে বারো হাল, পহ্র অরে এক হার-ও নেই অর্থাৎ রাতে বার হাল সকালে এক হাল-ও নাই। ধরুন, আপনি একটা কাজ করবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন। সেই পরিকল্পনা আপনার মনের মধ্যে শক্ত অবস্থানে মিলন ঘটালেন, বনাবনি করলেন এবং মনের মধ্যে পালন করলেন এ’টীই হচ্ছে মূল। এভাবে পরিকল্পনা মনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে মনের মধ্যে পালন করতে পারলে আপনি অবশ্যই সকালে হালচাষ করতে পারবেন। কিন্তু, যদি পরিকল্পনা মনের মধ্যে মিলন ঘটাতে না পারেন, পালন করতে না পারেন তাহলে সকালে হালচাষ করতে পারবেন না। ঘরে পাণি রাখতে হলে অবশ্যই কলসী প্রয়োজন। তাই পাণির জন্য কলসী হচ্ছে মূ। পরিকল্পনার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন মন। এই মন হচ্ছে পরিকল্পনার মূ। সুতরাং মুল বিজু মানে হচ্ছে দিক নির্ণয় করতে পারা এবং দিক নির্ণয় করতে পারার প্রতিফলন হচ্ছে মূল বিজু।
গজ্যেপজ্যে দিন:
√গ + জ্ + এ/ে + য = গামী + জনন + দিশাগ্রস্তন + যায়ী/যে যায়/যাহাতে।
√প + জ্+ এ/ে + য = পায়ী + জনন + দিশাগ্রস্তন + যায়ী/যে যায়/যাহাতে।
√দ্ + ই/ি + ন = দান + সক্রিয়ন/গতিশীল + নাকৃত-অনকৃত।
গজ্যেপজ্যে শব্দকে নিয়েও এক মহাসমস্যা। গজ্যেপজ্যে মানে এক্ষণ আমরা বুঝি গড়িয়ে পড়া, শুয়ে পড়া। এর চেয়ে বেশী আর কিছু বুঝি না। জাতীয় উৎসবের একটা দিন, সেই জাতীয় উৎসব গড়িয়ে পড়া, শুয়ে পড়া হবে কিসের উদ্দেশ্যে? উৎসবের দিনে গড়িয়ে পড়া, শুয়ে পড়া কী হয়? একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অবাক হতে হয় জাতীয় উৎসব কিভাবে গড়িয়ে পড়া, শুয়ে পড়া হয়? যাক এক্ষণ আমরা ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থ বিধির সাহায্যে গজ্যেপজ্যে দিনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।
গজ্যে এবং পজ্যে হচ্ছে দুটা শব্দ। দুটা শব্দ মিলে গজ্যেপজ্যে। গজ্যে এর ক্রিয়ামূল গড়্ মানে (গ) গামীর (ড়্) ডয়নরহস্য (চাকমা ভাষায় ড়-এর কাজ র বর্ণ দিয়ে হয়,র্ -এর অর্থ রক্ষণ, র-এর অর্থ রক্ষক)। পজ্যে-এর ক্রিয়ামূল পত্ মানে প/পায়ীর (সত্ত্বার পালন-পানের)ত/তারণ। অতএব, গজ্যে মানে গামীর জনন, দিশাগ্রস্তন যাহাতে)। গমনের মাঝেও জনন/জন্ম থাকে। নতুন কোথাও গেলে অজানাকে জানা যায়, তাই এখানেও জনন ক্রিয়া।গজ্যে(√গ + জ্ + এ্/ে + য = গামী + জনন + দিশাগ্রস্তন + যায়ী/যে যায়/যাহাতে)। এবং পজ্য মানে পায়ীর জনন দিশাগ্রস্তন যাহাতে (√প + জ্ + এ্/ে + য = পায়ী + জনন + দিশাগ্রস্তন + যায়ী/যে যায়/যাহাতে)। তারমানে, আপনি কল্পনা করতেছেন যে, জ্ঞানে, চেতনায় এবং কাজের কর্র্ম্মযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছেন এবং সেই শ্রমের ফলে জীবন বাঁচাচ্ছেন। ধরুন, আপনি কল্পনায় ধান চাষ করতেছেন। সেই কল্পনা চিত্র অংকন করে গজ্যেপজ্যে উৎসব আয়োজন করলেন। পূর্ব্বপুরুষরা এই নিয়মে বিজু উৎসব পালন করেছিলেন। সুতরাং গজ্যেপজ্যে মানে হচ্ছে কর্ম্মযজ্ঞে লিপ্ত হয়ে জীবন বাঁচা। এবং কর্ম্মযজ্ঞে লিপ্ত হয়ে জীবন বাঁচানোর প্রতিফলন হচ্ছে গজ্যেপজ্যে দিন।
সাংগ্রাই, বৈসুক, বিজুর বৈশিষ্ট্য যেহেতু একই সেহেতু সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিজু এবং বিহু উৎসবটী আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা উপরোক্ত নিয়মে পালন করেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। …
তথ্যসূত্র:
১. কলিম খান, দিশা থেকে বিদিশায়: নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশ বার্তা, (কলকাতা: হাওয়া ঊনপঞ্চাশ প্রকাশনী ১৪০৬ বাংলা) পৃ: ১৩
২. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গঁতীর্থে মুক্তি স্নান: বাংলাভাষা থেকে সভ্যতার ভবিতব্যে (কলকাতা: বঙ্গযান প্রকাশনী, ২০১৫) পৃ: ৮৩
৩. কলিম খান, পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন: ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং, অফবিট পাবলিশিং (কলকাতা: শ্যামল ধর, শুভদীপ কর্তৃক প্রকাশিত ২০০২) পৃ: ৩০
৪. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গঁতীর্থে মুক্তি স্নান: বাংলাভাষা থেকে সভ্যতার ভবিতব্যে (কলকাতা: বঙ্গযান প্রকাশনী, ২০১৫) পৃ: ৮৩
৫. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ দ্বিতীয় খন্ড, (কলকাতা: ভাষাবিন্যাস, ১৪১৭ বাংলা) পৃ: ৩৬
৬. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান), দ্বিতীয় খন্ড, (কলকাতা: ভাষাবিন্যাস, ১৪১৭ বাংলা) পৃ: ৫৭১
৭. সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি(জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত), অরুণা প্রকাশন সংস্করণ (কলকাতা: শ্যামল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১০) পৃ: ১৫২-১৫৩
৮. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান), দ্বিতীয় খন্ড, (কলকাতা: ভাষাবিন্যাস, ১৪১৭ বাংলা) পৃ: ৫৭১
৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫৩
১০. (ক্রিয়াভিত্তিক বর্ণার্থ বিধি)বাঙ্লাভাষার বানান-সমস্যা সমাধানের পথ— কলিম খান-রবি চক্রবর্তী।
সুমঙ্গল চাকমা রচিত ও প্রকৃতিপুরুষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ, বিজুর অজানা কথা — প্রকৃতিপুরুষ বানান রীতিতে সম্পাদিত।